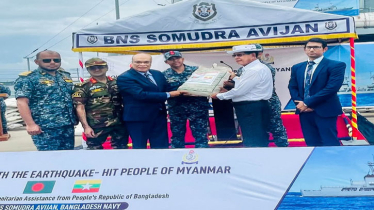গণমাধ্যম কোনো ঘটনার কেবল প্রতিফলন নয়; বরং ঘটনার অর্থ নির্মাণেও সক্রিয় ভূমিকা রাখে। Framing Theory অনুসারে সংবাদমাধ্যম যখন কোনো বিষয় উপস্থাপন করে, তখন তারা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যাখ্যার কাঠামোর মাধ্যমে পাঠকের উপলব্ধি গড়ে তোলে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষাপটে ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে সংবাদ কাভারেজে পরিবর্তন, এই তত্ত্ব বিশ্লেষণের যথাযথ ক্ষেত্র।
২০২৪ সালের ১৭ এপ্রিল, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়, দৈনিক সমকাল মুজিবনগর দিবসকে গুরুত্ব ও আবেগ দিয়ে কাভার করেছিল—শিরোনামে ছিল জাতির ইতিহাস, কাভারেজে ছিল রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর বাণী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।
অন্যদিকে ২০২৫ সালে সরকার পরিবর্তনের পর, একই দিবসের সংবাদ কাভারেজ ছিল সংক্ষিপ্ত, আবেগহীন, এবং রাষ্ট্রীয় বাণীবিহীন। ফ্রেমিং বদলে যায়—মুজিবনগর দিবস গুরুত্ব হারায়, সংবাদ হয়ে ওঠে নিছক একটি ‘দিনের’ উল্লেখমাত্র।
ফ্রেমের রাজনৈতিক ইঙ্গিত: গণমাধ্যমের Framing Theory অনুযায়ী, সংবাদমাধ্যম ঘটনা বাছাই ও উপস্থাপনে যেভাবে কিছু দিককে জোর দিয়ে এবং কিছু দিককে বাদ দিয়ে ফ্রেম তৈরি করে, তা সমাজে সেই ঘটনার অর্থ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই ফ্রেম অনেক সময় রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন হয়ে ওঠে। এই ফ্রেম পরিবর্তন প্রমাণ করে সংবাদমাধ্যম কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, বরং ক্ষমতার কাঠামো অনুযায়ী ফ্রেম পুনর্গঠন করে। এটি "regime-sensitive framing"-এর উদাহরণ, যেখানে রাজনৈতিক পালাবদল ‘মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক ইতিহাসের বয়ান’কেও ছাঁটাই করে।
ফলে প্রশ্ন জাগে—এই পরিবর্তন কি সত্যিকারের গণঅভ্যুত্থান, নাকি শুধু এক ধরনের রেজিম চেঞ্জ, যেখানে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বয়ান আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে? Framing Theory-এর আলোকে দেখা যায়, ১৭ এপ্রিলের এই সংবাদ কাভারেজে পার্থক্য কেবল সাংবাদিকতার নয়, বরং ইতিহাস, রাজনীতি ও আদর্শিক অবস্থানের প্রতিচ্ছবি। সংবাদমাধ্যম যখন ক্ষমতার পালাবদলে ফ্রেম পাল্টায়, তখন তা ইতিহাসচর্চা ও গণতন্ত্র উভয়ের জন্যই চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে।
গত বছরের আগস্টে মানুষ একটি অজনপ্রিয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসনকে প্রবল গণরোষে উচ্ছেদ করেছিলো। কিন্তু সেই পরিবর্তনের সাথে সাথে 'বয়ান' যখন এভাবে বদলে যায়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে - বাংলাদেশে কি 'গণঅভ্যুত্থান' হলো? নাকি 'মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির নেতৃত্বে রেজিম চেঞ্জ' হলো?